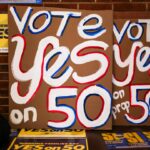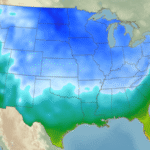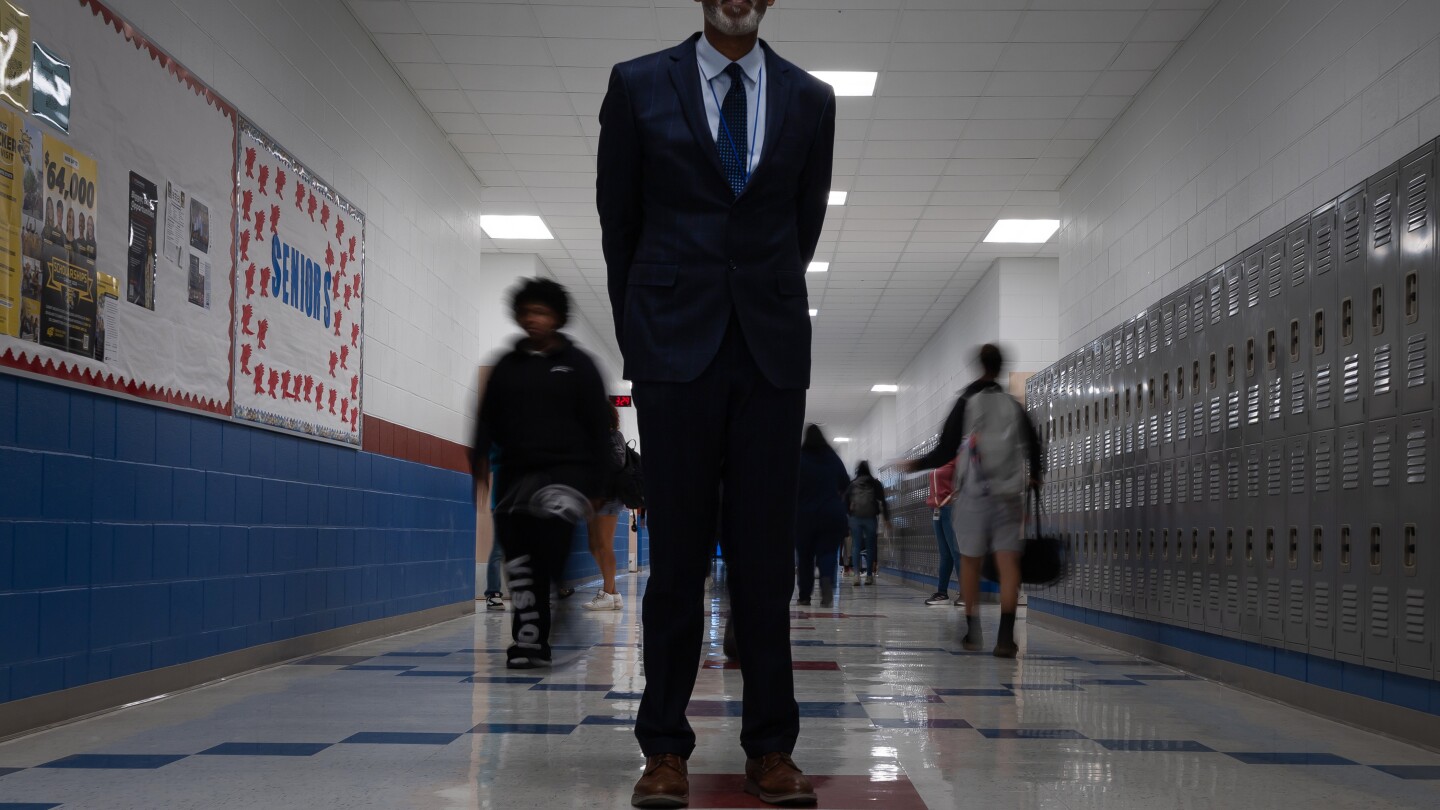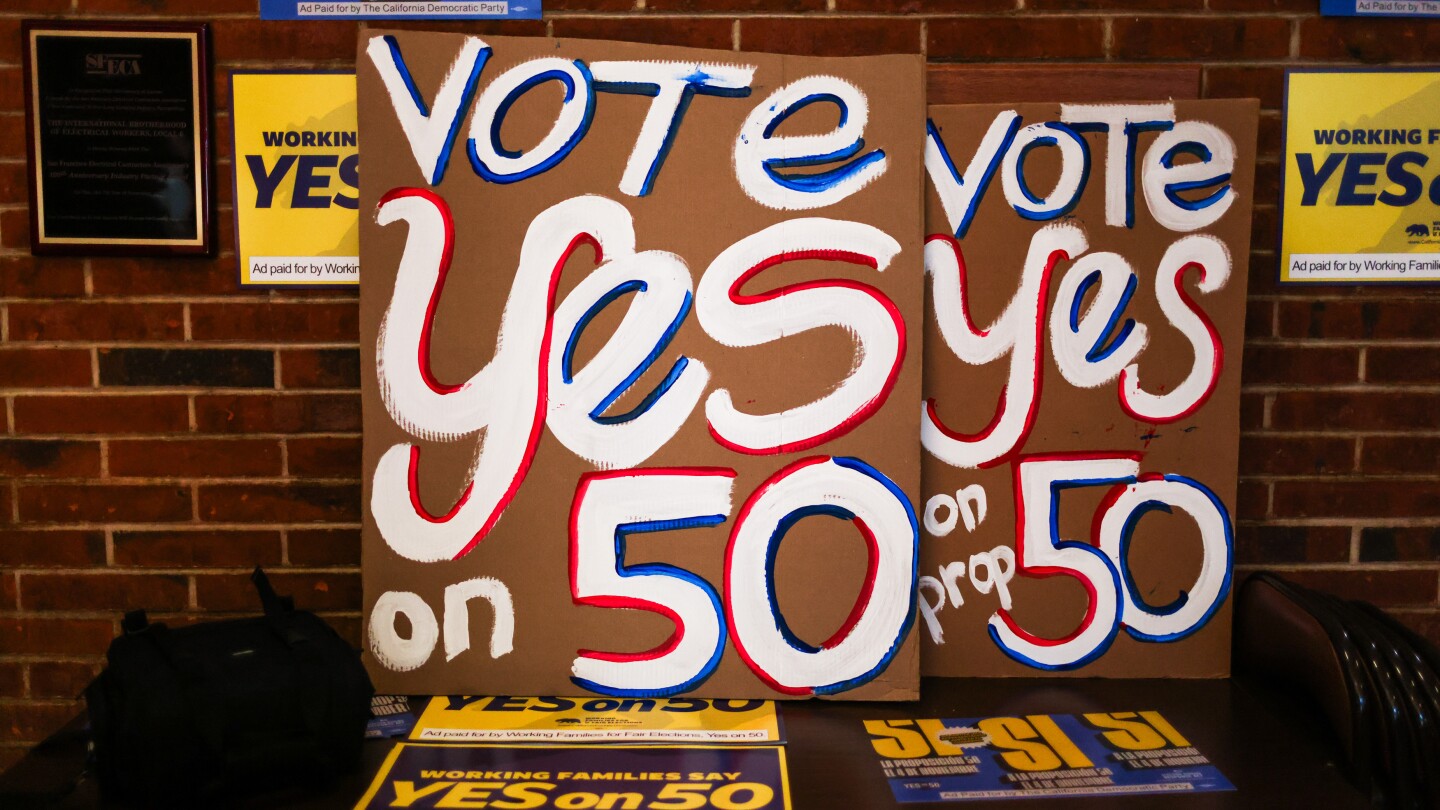যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নীতি: ট্রাম্পের শুল্ক ব্যর্থ, পুরনো পথে নেই মুক্তি
সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নীতি নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে চীনের উপর আরোপিত শুল্কের ফল ভালো হয়নি, বরং তা বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা তৈরি করেছে।
সম্প্রতি জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয় দেশই তাদের শুল্কের পরিমাণ কমানোর বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে।
মে মাসের শুরুতে দুই দেশের মধ্যে শুল্ক কমানোর বিষয়ে একটি চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই আলোচনা এখনো পর্যন্ত কোনো ফলপ্রসূ রূপ নেয়নি।
ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মার্কিন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা এবং দেশের শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।
কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, শুল্কের কারণে মার্কিন ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক কোম্পানি তাদের মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা কমাতে বাধ্য হয়েছে এবং দেশের জিডিপিও (মোট দেশজ উৎপাদন) কমে গেছে।
বিষয়টি পরিষ্কার যে, শুল্ক আরোপ করে মার্কিন শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব নয়, কিংবা দেশটিতে উৎপাদন শিল্প ফিরিয়ে আনাও সহজ নয়।
ট্রাম্প প্রশাসন এখন তাদের কৌশল পরিবর্তনের চেষ্টা করছে।
তবে, ‘স্থিতিশীলতা’র নামে পুরনো অর্থনৈতিক উদারীকরণের পথে ফেরাটাও সঠিক সমাধান নয়।
আসলে, বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে ধনী দেশগুলোর নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসেছে।
এই নীতিগুলোর কারণেই বিশ্ব আজ নানা ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি একটি নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরির চেষ্টা করেছিল, যেখানে বাণিজ্য, শ্রম এবং উন্নয়নের সেরা দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।
কিন্তু পরবর্তীতে, বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলোর বিরোধিতার কারণে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।
এই সময়টাতে, শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতি নমনীয়তা এবং অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়ের কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গিয়েছিল।
১৯৮০-এর দশকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের নেতৃত্বে কর্পোরেটদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
এর মধ্যে ছিল ধনী ব্যক্তিদের জন্য কর কমানো, আন্তর্জাতিক পুঁজির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে দুর্বল করা।
এর ফলস্বরূপ, উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য শ্রম-বহিষ্কার, কর ফাঁকি, জমির ব্যবসা এবং ফিনান্সিয়াল কারবার বেড়ে যায়।
উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) চাপ সৃষ্টি করে সরকারি ব্যয় কমাতে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলোর বেসরকারিকরণ করতে এবং বাজারের নিয়ন্ত্রণ দ্রুতভাবে তুলে দিতে।
এর ফলস্বরূপ, ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে অনেক দেশের জন্য উদার অর্থনীতির পথে যাত্রা ছিল একটি কঠিন অভিজ্ঞতা।
এই নীতিগুলোর কারণে কর্মসংস্থান কমে যায়, বৈষম্য বাড়ে এবং ঋণের বোঝা বাড়ে।
তবে, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো, যারা উদার অর্থনীতির সীমাবদ্ধতাগুলো এড়িয়ে নিজেদের মতো করে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।
এই ব্যবস্থার প্রধান সুবিধাভোগী ছিল পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলো।
কারণ, তারা কম খরচে পণ্য উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার মাধ্যমে লাভবান হয়েছিল।
কিন্তু পশ্চিমা শ্রমিকরা, যারা মজুরি কমে যাওয়া, কর্মসংস্থান হারানোর মতো সমস্যার শিকার হয়েছিলেন, তারা তেমন সুবিধা পাননি।
অতএব, ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতি যে ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।
একইভাবে, অর্থনৈতিক উদারতাবাদের পুরনো পথে ফিরে গেলেও সমস্যার সমাধান হবে না।
২০০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পর, পশ্চিমা সরকারগুলো ব্যাংকগুলোকে বাঁচিয়েছিল এবং বাজারের পুরনো ব্যবস্থাই বহাল রেখেছিল।
এর ফলে, জার্মানি থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাত্রার মান কমে যায়, মজুরি স্থিতিশীল হয়ে যায়, এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দুর্বল হয়ে পড়ে।
এখন প্রয়োজন একটি নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা বহু-পক্ষীয় সহযোগিতা, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং মানব-কেন্দ্রিক উন্নয়নের উপর জোর দেবে।
এই পদ্ধতিতে সরকারগুলোকে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর উপর কর আরোপ, ট্যাক্স haven বন্ধ করা, পুঁজির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা, শ্রম ও পরিবেশগত মান নির্ধারণ করা, সবুজ প্রযুক্তি বিনিময় করা এবং বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের জন্য অর্থায়নে সহযোগিতা করতে হবে।
উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশগুলোকে শিল্পনীতি বাস্তবায়নের সুযোগ দিতে হবে এবং সরকারি আর্থিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
উন্নত দেশগুলোকে ধীরে ধীরে ‘উত্তর-বৃদ্ধি মডেল’ গ্রহণ করতে হবে, যেখানে জিডিপি-র (GDP) ক্রমাগত বৃদ্ধির পরিবর্তে মানুষের কল্যাণ, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং সামাজিক সমতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
এর অর্থ হলো, স্বল্পমেয়াদী মুনাফা বা সম্পদ আহরণের পরিবর্তে, পরিচর্যা বিষয়ক কাজ, সবুজ অবকাঠামো এবং জনসাধারণের পরিষেবাগুলোতে বিনিয়োগ করা।
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর লক্ষ্য হওয়া উচিত, বেশি উৎপাদনের পরিবর্তে ভালো বিতরণ নিশ্চিত করা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবন যাপন করা।
এর ফলে, স্বল্প ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারবে, যা সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে না।
সরকারগুলো কর্পোরেশনগুলোর উপর কর আরোপ ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারলে, তারা স্থিতিশীল ও ভালো বেতনের চাকরি তৈরি করতে, শ্রমিক সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করতে এবং বৈষম্য কমাতে সক্ষম হবে।
এটি মার্কিন শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রার মান ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায়।
এ ধরনের প্রগতিশীল বহু-পক্ষীয়তা, অগণতান্ত্রিক জনতাবাদকে (illiberal populism) প্রতিরোধের দীর্ঘমেয়াদী হাতিয়ার হতে পারে।
তবে, এই পরিবর্তন আনতে হলে বিদ্যমান কর্পোরেট স্বার্থের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং পুঁজিবাদ-নির্ভর বিশ্ব কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক জোট তৈরি করতে হবে।
সুতরাং, ট্রাম্পের ধ্বংসাত্মক নীতির সমালোচনা করার পাশাপাশি, শিল্পখাতে নতুনত্ব, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচারের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।
আগামী মাসগুলোতে দেখা যাবে, এই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে কেউ প্রস্তুত কিনা।
তথ্য সূত্র: আল জাজিরা