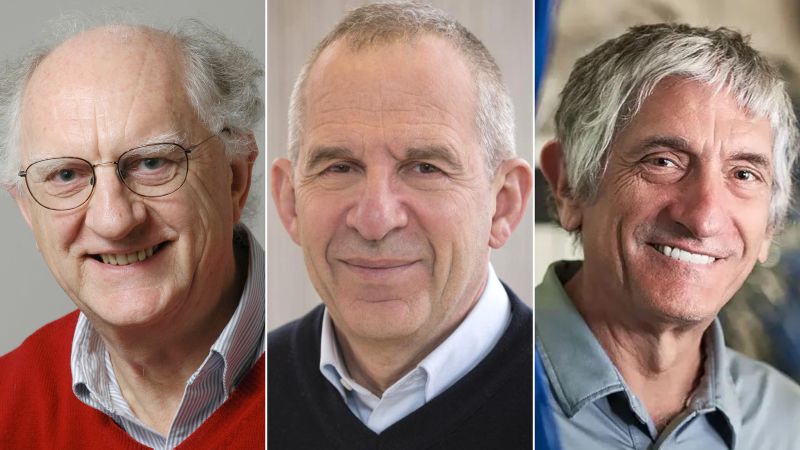একটি বিশাল জীবন্ত কাঠামো, যা পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান, সেটি হলো অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট বেরিয়ার রিফ। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই প্রবাল প্রাচীর আজ হুমকির সম্মুখীন। গত কয়েক বছরে এখানে ব্যাপকহারে প্রবাল “ব্লিচিং”-এর ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে এর রঙিন জীবন্ত রূপ সাদা হয়ে যাচ্ছে।
এই ঘটনা শুধু গ্রেট বেরিয়ার রিফের একার নয়, সারা বিশ্বের সমুদ্রের প্রবালগুলিতেও একই বিপদ দেখা দিয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে সমুদ্রের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে ৮০ শতাংশেরও বেশি প্রবালের ক্ষতি হয়েছে। এই “ব্লিচিং”-এর কারণে প্রবালের ভেতরের শৈবালগুলো দুর্বল হয়ে যায়, যা তাদের খাদ্য সরবরাহ করে।
এর ফলস্বরূপ, প্রবালগুলো ধীরে ধীরে মারা যায়। সমুদ্রের তলদেশের মাত্র ০.০১ শতাংশ স্থান জুড়ে থাকা সত্ত্বেও, প্রবাল প্রাচীরগুলি সমুদ্রের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি জীবনের আশ্রয়স্থল।
এটি খাদ্য ও জীবিকারও উৎস, এছাড়াও ঝড় থেকে উপকূলকে রক্ষা করতে এবং ভূমি ক্ষয় রোধ করতে সহায়ক। জাতিসংঘের সমুদ্র সম্মেলনে, জলবায়ু-সহনশীল প্রবাল রক্ষার জন্য ১১টি দেশ অঙ্গীকার করেছে।
এছাড়াও, সরকার ও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাগুলি প্রবাল প্রাচীর বিষয়ক একটি বৈশ্বিক তহবিলে ২৫ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রবাল প্রাচীর রক্ষার জন্য কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে সমুদ্রের তাপমাত্রা কমানো জরুরি।
বিজ্ঞানীরা উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রবালকে টিকিয়ে রাখার জন্য অন্যান্য সমাধানও খুঁজছেন। সিডনির ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির (University of Technology Sydney) বিজ্ঞানীরা “সুপার কোরাল” (Super Corals) আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন।
তারা এমন প্রজাতি খুঁজছেন, যা উচ্চ তাপমাত্রা, অম্লতা বা কম অক্সিজেনের মতো পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে সহজে মানিয়ে নিতে পারে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, এই ধরনের প্রবাল সনাক্ত করা এবং তাদের টিকে থাকার কৌশল খুঁজে বের করা।
এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রবালকে প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচতে সহায়তা করা যাবে। ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী এবং “ফিউচার রিফ” (Future Reefs) দলের প্রধান ড. এমা ক্যাম্প বলেন, “আমরা একটি পরিবর্তনশীল পরিবেশে প্রবালের টিকে থাকার বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছি।
কীভাবে আমরা প্রবালকে আরও শক্তিশালী করতে পারি, যাতে তারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও টিকে থাকতে পারে? একইসঙ্গে, মানুষ হিসেবে আমরা কীভাবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ব্যবহার করে প্রবালকে আরও শক্তিশালী করতে পারি?” গবেষকরা জানান, তারা এরই মধ্যে বিভিন্ন পরিবেশে ৪০টির বেশি “সুপার কোরাল” প্রজাতি খুঁজে পেয়েছেন।
বর্তমানে গ্রেট বেরিয়ার রিফের মধ্যে তারা এই ধরনের প্রবাল খুঁজছেন। গবেষক দলের পোস্টডক্টরাল গবেষক ক্রিস্টিন রোপার বলেন, “আমরা এমন প্রবাল প্রজাতি সনাক্ত করতে চাই, যাদের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেশি।
একইসঙ্গে, তারা যেন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে এবং অন্যান্য জীবের বসবাসের জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করতে পারে।” গ্রেট বেরিয়ার রিফে অভিযান চালিয়ে গবেষক দল নির্দিষ্ট প্রবাল প্রজাতি সংগ্রহ করে সেগুলির বিশ্লেষণ করেন।
তারা একটি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রবালের টিকে থাকার সম্ভাবনা পরীক্ষা করেন। এছাড়াও, তারা ল্যাবে নিয়ে আসার জন্য প্রবালের কিছু অংশ সংগ্রহ করেন, যেখানে ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়।
একবার কোনো চাপ-সহনশীল প্রজাতি সনাক্ত করা গেলে, “কোরাল নার্চার প্রোগ্রাম” (Coral Nurture Program)-এর মাধ্যমে সেগুলিকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়। এই প্রোগ্রামের অধীনে স্থানীয় পর্যটন অপারেটর এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করা হয়।
২০১৮ সাল থেকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রেট বেরিয়ার রিফে ১ লক্ষ ২৫ হাজারের বেশি প্রবাল প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮৫ শতাংশ এখনো টিকে আছে। তবে, গ্রেট বেরিয়ার রিফের মতো বিশাল অঞ্চলে এই ধরনের কাজ করা সহজ নয়।
এই রিফে প্রায় ৩,০০০টি আলাদা প্রবাল প্রাচীর রয়েছে এবং এর আয়তন প্রায় ৩,৪৪,৪০০ বর্গকিলোমিটার। এপ্রিল ২০২৪ সাল পর্যন্ত, এর প্রায় ৬০ শতাংশ প্রবালের সম্ভাব্য “ব্লিচিং”-এর শিকার হওয়ার আশঙ্কা দেখা গেছে।
গবেষকরা আশা করছেন, যেখানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, সেখানকার অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য গবেষণাগারেও একই ধরনের সমাধান নিয়ে কাজ চলছে।
অস্ট্রেলিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেরিন সায়েন্স (Australian Institute of Marine Science – AIMS) তাপ-সহনশীল প্রবাল তৈরি করতে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করছে। তারা জানিয়েছে, জেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া গেছে, তবে প্রজাতিভেদে এর সাফল্য ভিন্ন।
যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ও (University of Newcastle) এমন প্রবাল তৈরি করেছে, যা সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি ভালোভাবে সহ্য করতে পারে। ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে প্রবাল পুনরুদ্ধার কয়েক বছরের মধ্যে ব্যর্থ হতে পারে, যদি আবার “ব্লিচিং”-এর ঘটনা ঘটে।
তবে তাপ-সহনশীল প্রবাল রোপণ করে “কোরাল নার্চার প্রোগ্রাম” আশা করছে, ভবিষ্যতে এই পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া টিকে থাকবে। ক্রিস্টিন রোপার বলেন, “আমরা তাপ-সহনশীল প্রবালের সংখ্যা বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছি, যাতে ভবিষ্যতে তারা তাপমাত্রার চাপ সহ্য করতে পারে।”
প্রাকৃতিকভাবে হোক বা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হোক, এই প্রবাল রোপণের প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। এর জন্য ডুবুরিদের রিফে নেমে হাতে করে প্রবাল লাগাতে হয়।
এজন্যই “কোরাল নার্চার প্রোগ্রাম” পর্যটন অপারেটর ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করছে। ড. ক্যাম্প বলেন, “আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই কাজের পরিধি বাড়াতে পারি।” এই প্রোগ্রামটি গ্রেট বেরিয়ার রিফের সাতটি পর্যটন অপারেটরের সঙ্গে সহযোগিতা করে।
এর মধ্যে “ওয়েভলেংথ রিফ ক্রুজ” (Wavelength Reef Cruises) অন্যতম। পর্যটকদের রিফ ভ্রমণের টিকিট কাটার পাশাপাশি, এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রবাল প্রতিস্থাপনের কাজও করা হয়। এই ক্রু সদস্যরা প্রশিক্ষিত ডুবুরি এবং সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী।
তারা প্রবাল প্রতিস্থাপন, নার্সারি রক্ষণাবেক্ষণ এবং এলাকার সমীক্ষার মতো কাজ করে। ওয়েভলেংথ-এর কর্মীরা ড. ক্যাম্পের সঙ্গে এই প্রোগ্রাম শুরু করতে সাহায্য করেছে এবং রিফে প্রবাল নার্সারি পরিচালনা ও প্রবালের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
তবে, কঠিন প্রিসিস (tough coral) প্রজাতির প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কতটা কাজ করা সম্ভব, তার একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। “ফিউচার রিফ” দল অন্যান্য সমাধানও খুঁজছে, যেমন – প্রবালকে বিভিন্ন ধরনের খাবার বা ভিটামিন সরবরাহ করা হলে তাদের তাপ সহনশীলতা বাড়ানো যেতে পারে কিনা।
অতীতে, “ব্লিচিং”-এর ঘটনার পর প্রবালের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে জুওপ্ল্যাঙ্কটন (zooplankton) – জলের উপরিভাগে ভেসে থাকা ক্ষুদ্র প্রাণী – সরবরাহ করে ভালো ফল পাওয়া গেছে। এছাড়াও, ম্যাঙ্গানিজ ও জিঙ্কের মতো ধাতব পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ স্থানে প্রবাল বৃদ্ধি করেও উপকার পাওয়া গেছে।
তবে, এই পদ্ধতিগুলো এখনো বৃহৎ আকারে পরীক্ষা করা হয়নি। ড. ক্যাম্প বলেন, “প্রবাল সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু জানা থাকলেও, তাদের পুষ্টি সম্পর্কে আমরা খুব কম জানি। আমার মনে হয়, গবেষণা ও বিজ্ঞান এই ক্ষেত্রে আমাদের পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে, কারণ এর মাধ্যমে প্রবালের প্রয়োজনীয়তাগুলো আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে।”
সিডনির পরীক্ষাগারে, গবেষকরা বিভিন্ন ধরনের শৈবাল মিশ্রিত মাইক্রোস্কোপিক ব্রাইন শ্রিম্প (microscopic brine shrimp) এবং কিছু ধাতু বা ভিটামিন যুক্ত করে প্রবালের খাদ্য তৈরি করছেন। তাদের লক্ষ্য হলো, এমন একটি পরিপূরক তৈরি করা যা চাপের মধ্যে থাকা প্রবালকে অতিরিক্ত পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে এবং ব্যাপক “ব্লিচিং”-এর ঘটনা থেকে তাদের বাঁচতে সাহায্য করবে।
ড. ক্যাম্প বলেন, “এটা অনেকটা আমাদের মতো। যখন আমরা দুর্বল বোধ করি, তখন শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য একটি পরিপূরক গ্রহণ করি। প্রবালের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য।” তিনি আরও বলেন, এই ধরনের সমাধান বিশ্বব্যাপী প্রবাল প্রাচীরে প্রয়োগ করা সহজ হবে।
তিনি যোগ করেন, “আমাদের এই ধরনের নতুন ধারণাগুলো অন্বেষণ করতে হবে, কারণ আমরা যদি কিছু না করি, তাহলে সারা বিশ্বের প্রবাল প্রাচীরগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।” বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং কার্যকরী সমাধানের মাধ্যমে প্রবাল প্রাচীর রক্ষার চেষ্টা করা হলেও, ড. ক্যাম্প সতর্ক করে বলেন, দীর্ঘমেয়াদে তাদের রক্ষার মূল চাবিকাঠি হলো ব্যাপক প্রবাল “ব্লিচিং”-এর কারণগুলো মোকাবেলা করা, যা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা কমানোর ওপর নির্ভরশীল।
তিনি বলেন, “আমরা প্রবাল প্রাচীরকে বাঁচানোর জন্য কেবল কিছু সময়ের জন্য চেষ্টা করতে পারি। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করতে হবে, কারণ তাপমাত্রা যদি বাড়তেই থাকে, তাহলে তাদের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।” তথ্য সূত্র: সিএনএন