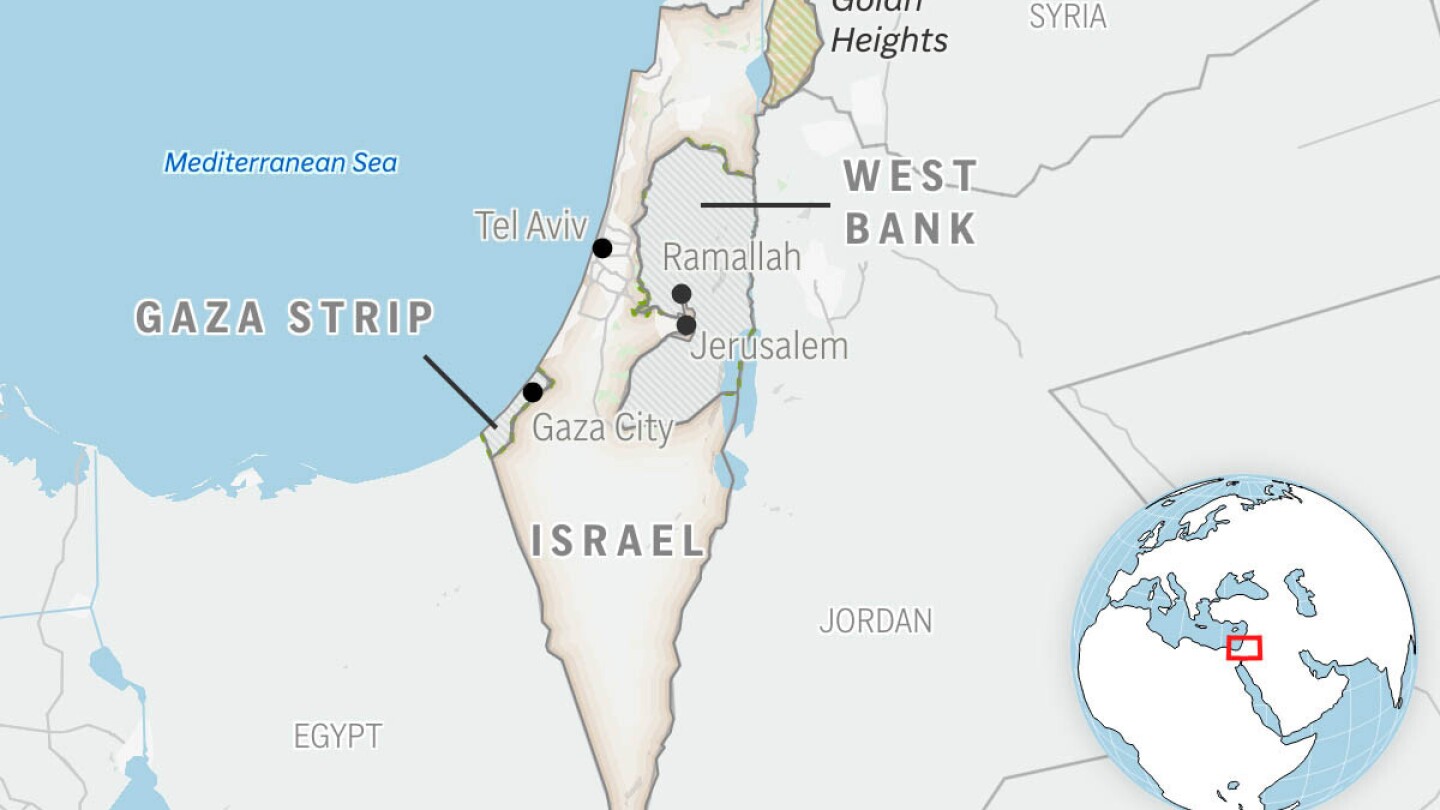জাপানের ইতিহাসে ‘সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে’ শিন্টো ধর্মের উত্থান ঘটেছিল, এরপর থেকে দেশটির সংস্কৃতিতে যোদ্ধাদের এক বিশেষ স্থান ছিল। এই যোদ্ধাদের ‘সামুরাই’ বলা হতো, যাদের বীরত্ব, আনুগত্য এবং আত্মত্যাগের আদর্শ জাপানি সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।
তবে, সময়ের সাথে সাথে এই সামুরাইদের জীবনেও আসে পরিবর্তন। এক সময়ের পরাক্রমশালী এই যোদ্ধাদের জীবন কিভাবে বদলে গেল, সেই গল্পই আজ আমরা জানবো।
হেইয়ান যুগে (৭৯৪-১১৮৫) সামুরাইদের উত্থান হয়, যখন তারা অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে মিশে সমাজে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এরপর ওনিন যুদ্ধসহ বিভিন্ন বিদ্রোহে তাদের বীরত্ব প্রদর্শিত হয়।
এরপর, বুশি নামে পরিচিত এই যোদ্ধারা জাপানের ইতিহাসে নিজেদের স্থান করে নেয়, যা জাপানি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।
তবে, সামুরাইদের স্বর্ণযুগ ধরা হয় টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের সময়কে (১৬০৩-১৮৬৮), যা এডো পিরিয়ড নামেও পরিচিত। এই সময়টা ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি, এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের কাল।
এই সময়ে সাহিত্য, সিনেমা এবং কমিক্সেও সামুরাইদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু, অনেকের মতে, এটি ছিল সামুরাই সংস্কৃতির অস্তমিত হওয়ার শুরু।
টোকুগাওয়া regime-এর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর, ১৬১৫ সালে ওসাকা দুর্গের পতনের মধ্য দিয়ে জাপানে দীর্ঘ শান্তির সূচনা হয়। যদিও মাঝে মাঝে কিছু কৃষক বিদ্রোহ দেখা গেছে, তবে উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধ হয়নি।
১৬৩৮ সালের শিমাবারা বিদ্রোহ ছিল এর একটি উদাহরণ, যা ছিল অতিরিক্ত কর এবং খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতনের ফল। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন আমাকুসা শিরো নামের এক খ্রিস্টান সামুরাই।
ডাচ বণিকদের সরবরাহ করা কামান ব্যবহার করে সরকারি বাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে।
এই ঘটনার পর, তৃতীয় টোকুগাওয়া শোগুন ইয়েমিцу বিদেশি প্রভাব থেকে দেশকে দূরে রাখতে ‘সাকোকু’ নামে পরিচিত একটি কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে জাপানে দুই শতাব্দীর বেশি সময় ধরে কোনো যুদ্ধ হয়নি।
কিন্তু এর খারাপ দিক ছিল, সামুরাইরা তাদের গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। হাজার হাজার সামুরাই, যাদের পূর্বপুরুষরা বহু বছর ধরে যুদ্ধ করেছে, তাদের এখন নতুন করে জীবন ধারণের পথ খুঁজতে হচ্ছিল।
শান্তির সময়েও কিছু সামুরাই তরবারি চালনায় নিজেদের দক্ষতা দেখিয়েছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন মিয়ামতো মুসাসি (১৫৮৪-১৬৪৫)। তিনি ১৬০০ সালের সেকিগাহারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কিনা, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।
মুসাসি পরে কোনো প্রভুর অধীনে কাজ না করে, নিজের ‘নি-তো-রিও’ কৌশল তৈরি করেন, যেখানে দুটি তরবারি ব্যবহার করা হতো। তিনি প্রায় ৭০টি দ্বৈরথে অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রতিটিতেই জয়ী হয়েছিলেন।
মৃত্যুর আগে তিনি ‘গোরিন নো শো’ নামে একটি বিখ্যাত যুদ্ধকৌশল বিষয়ক বই লেখেন।
১৭ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দ্বৈরথ নিষিদ্ধ করা হয় এবং আত্মরক্ষার জন্য কেবল তরবারি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে, সামুরাইরা প্রতিপক্ষকে আগে আক্রমণ করতে প্ররোচিত করতে শুরু করে, যাতে আত্মরক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়।
অনেকেই ‘আইআইজুুৎসু’ কৌশল আয়ত্ত করেন, যেখানে দ্রুত তরবারি বের করে প্রতিহত করা যেত। এই সময়ে ‘কেনজুুৎসু’ থেকে ‘আইআইজুুৎসু’-এর জনপ্রিয়তা বাড়ে, এবং বিভিন্ন ডজো বা মার্শাল আর্ট স্কুলে এর চর্চা শুরু হয়।
সামুরাইদের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ‘রোনিন’-এর উদ্ভব হয়, অর্থাৎ সেই সামুরাই যারা তাদের প্রভু হারিয়েছিল। ‘রোনিন’ শব্দটির অর্থ হলো ‘তরঙ্গের মানুষ’, যা উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো এবং অনিশ্চয়তার প্রতীক।
রোনিনদের নিয়ে একটি রোমান্টিক ধারণা তৈরি হয়েছিল, তাদের দুঃসাহসিক হিসেবে দেখা হতো। মিয়ামতো মুসাসি ছিলেন এর উজ্জ্বল উদাহরণ।
তবে, অধিকাংশ রোনিনই ছিল ভবঘুরে, এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের দেহরক্ষী, প্রহরী বা সাধারণ শ্রমিকের মতো কাজ করতে হতো।
অন্যদিকে, এডো (বর্তমান টোকিও) শহরে সবকিছু দ্রুত উন্নতি লাভ করছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরটি ধনী ও জনবহুল হয়ে ওঠে, যা বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
জার্মান চিকিৎসক এঙ্গেলবার্ট কেম্পফার এডোকে ‘পৃথিবীর কেন্দ্র’ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। এই সমৃদ্ধির কারণ ছিল, সামন্ত প্রভুদের বছরে ছয় মাস এডোতে বসবাস করতে হতো, ফলে তাদের সামুরাই এবং অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে এখানে থাকতে হতো।
অনেক রোনিনও এডোতে এসে ভিড় জমায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ অপরাধ জগতে প্রবেশ করে, চাঁদাবাজি ও পতিতাবৃত্তির মতো কাজ শুরু করে। ধীরে ধীরে তারা ‘ইয়াকুজা’ নামে পরিচিত হয়, যা অনেকটা জাপানি মাফিয়ার মতো ছিল।
তাদের অস্ত্র, ট্যাটু এবং পোশাক তাদের আলাদা পরিচয় দিত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করত।
যেসব সামুরাই ‘দাইমিও’ বা সামন্ত প্রভুদের অধীনে কাজ করত, তাদের বছরে কিছু সময় রাজধানীতে প্রভুর সঙ্গে কাটাতে হতো। সেখানে তারা সামান্য বেতন পেত এবং প্রভুর সম্পত্তির দেখাশোনার মতো কাজ করত।
তাদের সামাজিক নিয়মের কারণে ব্যবসা বা বিনিয়োগ করার সুযোগ ছিল না, ফলে তাদের আর্থিক অবস্থা প্রায়ই খারাপ থাকত।
অনেকে মদের দোকানে সময় কাটাতো এবং ‘ইয়োশিওয়ারা’-র মতো বিনোদন কেন্দ্রে যেত। অনেক পুরনো বংশের সামুরাই, মেয়েদের ‘মিজউইজ’ (যৌন সঙ্গম) খরচ যোগানোর জন্য তাদের ‘কাটানা’ বিক্রি করতে বাধ্য হতো।
তবে, সব সামুরাই এই ধরনের জীবন যাপন করত না।
কিছু সামুরাই আবার শিল্পের জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাতসুও বাঁশো (১৬৪৪-১৬৯৪), যিনি জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাইকু কবি ছিলেন। তিনি ছিলেন এক পুরনো সামুরাই পরিবারের সন্তান।
চিত্রকলার জগতে ওয়াতানাবে কাযান (১৭৯৩-১৮৪১) এবং কাওয়ানাবে কিওসাই (১৮৩১-১৮৮৯)-এর মতো শিল্পীরাও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।
কিছু সামুরাই টোকুগাওয়া শোগুনদের দরবারে মন্ত্রী ও আমলা হিসেবে ক্ষমতা লাভ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন কিরা ইয়োশিনাকা (১৬৪১-১৭০৩)। দায়িমিয়ো আসানো নাগানোরির সঙ্গে তার বিরোধের জেরে আসানোকে ‘সেপ্পুকু’ বা আত্মহত্যার মাধ্যমে শাস্তি পেতে হয়।
এর ফলস্বরূপ, ‘৪৭ রোনিনের প্রতিশোধ’-এর ঘটনা ঘটে। আসানোর মৃত্যুর পর, তার অনুগত সামুরাইরা রোনিনে পরিণত হয় এবং এক বছর পর কিরাকে হত্যা করে তাদের প্রভুর প্রতিশোধ নেয়। পরে তাদেরও ‘হারা-কিরি’ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামুরাই, শোগুন টোকুগাওয়া ইয়েয়াসুর বিজয়, তার নিজের সম্প্রদায়ের পতনের সূচনা করে। ‘বুশি’র আচরণবিধি আগের মতো গুরুত্ব হারায়, এবং সামুরাইদের একটি আদর্শায়িত চিত্র তৈরি হয়, যা বাস্তবে ছিল না।
উনিশ শতকে, যখন জাপান বিদেশি শক্তির দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন সামুরাইদের পুরনো আদর্শের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। আজও জাপানে সামুরাই ঐতিহ্যের কিছু প্রভাব দেখা যায়, যেমন সামরিক সংস্কৃতি, ইয়াকুজার কার্যকলাপ, এবং শৃঙ্খলা ও শৈল্পিকতার মতো গভীর মূল্যবোধ।
‘হাগাকুরে’ হলো ১৮ শতকে ইয়ামামোতো তসুনোতোমোর লেখা একটি সংকলন, যেখানে সামুরাইদের নৈতিকতা ও জীবন-দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি ‘ইন দ্য শেড অফ লিভস’ বা ‘ফলেন লিভস’ নামেও পরিচিত।
এটি সেই সময়ের কথা বলে, যখন সামুরাইরা তাদের যোদ্ধাচিত জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। ইয়ামামোতো ছিলেন একজন পণ্ডিত, যোদ্ধা এবং লাইব্রেরিয়ান। তিনি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে এই বই লেখেন, যেখানে মৃত্যু, আনুগত্য এবং প্রতিকূলতার মধ্যে শান্ত থাকার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।
তথ্য সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক