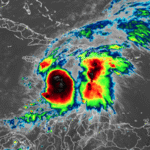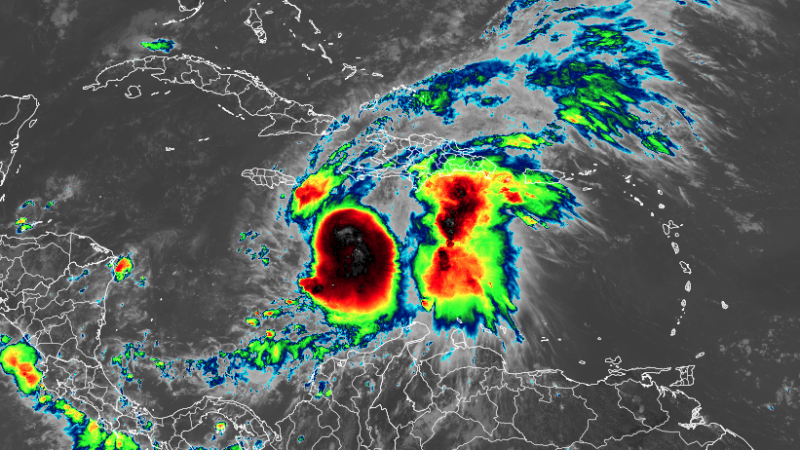রাজনৈতিক দায় এড়াতে এআই-এর দোষ চাপানোর প্রবণতা বাড়ছে: বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ।
বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে, একটি নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে—কোনো ঘটনার দায় এড়াতে সরাসরি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (এআই) দায়ী করা। বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় অথবা ভুল তথ্যের দায় থেকে বাঁচতে এখন প্রায়ই এআই-এর শরণাপন্ন হচ্ছেন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবণতা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ, যা জনসাধারণের মধ্যে সত্যের প্রতি আস্থা কমিয়ে দিতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক একটি মন্তব্য এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সম্প্রতি, একটি ভিডিওতে দেখা যায়, হোয়াইট হাউসের জানালা থেকে কিছু একটা বাইরে ফেলা হচ্ছে।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, “সম্ভবত এটা এআই।” যদিও তার প্রেস টিম এর আগে জানিয়েছিল যে ভিডিওটি আসল।
ট্রাম্পের এই মন্তব্যের মাধ্যমে, তিনি যেন সরাসরি এআই-কে দোষারোপ করার এই নতুন ধারণাকে সমর্থন করলেন। এমনকি তিনি আরও যোগ করেন, ভবিষ্যতে কোনো খারাপ ঘটনা ঘটলে, তিনিও সম্ভবত এআই-কে দায়ী করবেন।
শুধু ট্রাম্পই নন, ভেনেজুয়েলার যোগাযোগমন্ত্রী ফ্রেডি নানেজও সম্প্রতি একটি ভিডিওর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যেখানে একটি মার্কিন হামলায় ভেনেজুয়েলার একটি গ্যাংয়ের সদস্য নিহত হয়।
নানেজ তার টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টে এই ভিডিওটিকে ‘কার্টুন চিত্রের মতো’ আখ্যা দিয়ে বলেন, সম্ভবত এটি এআই ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এআই-কে দোষারোপ করার এই প্রবণতা একদিকে যেমন উদ্বেগের, তেমনি এর কিছু বিপদও রয়েছে।
ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে’র অধ্যাপক এবং ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হানি ফরিদ দীর্ঘদিন ধরে এআই-এর মাধ্যমে তৈরি হওয়া ‘ডিপফেক’ ছবি, কণ্ঠস্বর এবং ভিডিওর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সম্পর্কে সতর্ক করে আসছেন।
তার মতে, সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, যখন যেকোনো কিছুই ‘নকল’ হতে পারে, তখন কোনো কিছুই আর ‘আসল’ নাও থাকতে পারে।
বোস্টন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ ল’র ড্যানিয়েল কে. সিট্রন এবং টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট চেসনি ২০১৯ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় ‘মিথ্যার বিভাজন’ বা ‘লায়ার্স ডিভিডেন্ড’-এর ধারণা তুলে ধরেন।
তাদের মতে, যদি জনসাধারণের বিশ্বাস সত্য থেকে সরে যায় এবং সত্য একটি মতামতের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেই ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যাবে, যাদের মতামত সবচেয়ে প্রভাবশালী।
বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, অনেক মার্কিন নাগরিক এআই নিয়ে উদ্বিগ্ন। উদাহরণস্বরূপ, পিউ রিসার্চ সেন্টারের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক মার্কিনির মতে দৈনন্দিন জীবনে এআই-এর ব্যবহার তাদের মধ্যে উদ্বেগের জন্ম দেয়।
কুইননিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিপে দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীদের একটি বড় অংশ এআই-এর তৈরি তথ্যের ওপর খুব বেশি আস্থা রাখতে পারে না।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ট্রাম্পের এই ধরনের মন্তব্য এবং ‘মিথ্যা খবর’ প্রচারের ইতিহাস, মানুষের মধ্যে সত্যের প্রতি আস্থাহীনতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
ট্রাম্প এর আগেও বিভিন্ন সময়ে মিডিয়া রিপোর্টকে ‘ভুয়া খবর’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং সাংবাদিকদের ‘অসম্মানিত’ করার চেষ্টা করেছেন, যাতে তাদের নেতিবাচক খবর কেউ বিশ্বাস না করে।
এআই-কে দোষারোপ করার এই প্রবণতা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা, যা গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের মধ্যে আস্থার সম্পর্ককে দুর্বল করে দিতে পারে।
বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও, যেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার বাড়ছে, সেখানে এআই-এর অপব্যবহারের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়ছে।
তাই, রাজনৈতিক নেতাদের এআই-এর ব্যবহার সম্পর্কে আরও সতর্ক হওয়া উচিত এবং জনগণকে সত্য তথ্যের প্রতি সচেতন করতে হবে।
তথ্য সূত্র: আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম।